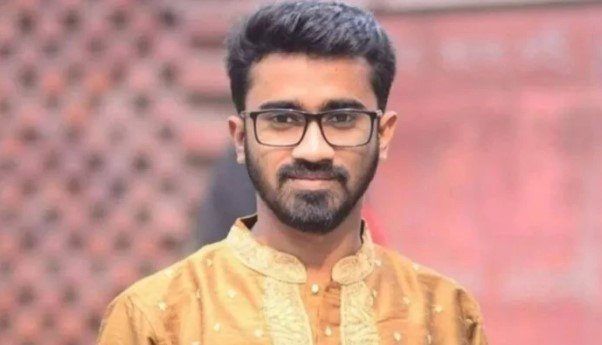"নতুন রাজনীতির নামে পুরোনো খেলা"

এই ভূখণ্ডের ইতিহাস আর তরুণ বিদ্রোহ সমান বয়সী। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রহেলিকা হলো, এখানকার তরুণেরা কখনো ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেননি। বিপুল সম্ভাবনা থাকার পরও তাঁরা কোনো বড় রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারেননি।
প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে দোষ কি শুধুই তরুণদের? নাকি দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও প্রচারমাধ্যম মিলিয়ে প্রথাগত ক্ষমতাকাঠামোর যে শক্তিশালী নেক্সাস এখানে গড়ে উঠেছে, সেই শক্তিই তরুণদের আত্মত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষাকে বারবার ব্যর্থ করেছে? ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, বিদ্রোহে তরুণেরা যতটা স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃজনশীল, কিন্তু গঠনের সময়টাতে ততটাই অসৃজনশীল ও হঠকারী। ইতিহাস কিন্তু এই প্রমাণও দেয় যে পুরোনো রাজনৈতিক-অর্থনীতির সুবিধাভোগীরা একদিকে যেমন তরুণদের তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে, অন্যদিকে স্বার্থের বিপরীতে গেলে দমন–পীড়ন চালাতেও কার্পণ্য করে না।
চব্বিশের অভ্যুত্থানে সাধারণ মানুষ ছাত্রদের নেতৃত্বের পেছনে সমবেত হওয়ার পেছনে দুটি বড় কারণ ছিল। প্রথমত, তারা শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল। দ্বিতীয়ত, ছাত্ররা ছিলেন তাদের কাছে একেবারে নতুন মুখ।
১৪ মাস আগে আমরা যদি ফিরে তাকাই, তাহলে দেখব যে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের নিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সমর্থন কতটা আকাশচুম্বী ছিল। অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মাথায় কুমিল্লা-নোয়াখালী-ফেনীর নজিরবিহীন বন্যায় ছাত্রদের খোলা ত্রাণশিবিরে সহযোগিতা উপচে পড়েছিল। কেউ সোনার অলংকার, কেউ মাটির ব্যাংকে জমানো টাকা নিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা পৌঁছে দিয়েছিল। প্রতিটি গল্পই ছিল আশাবাদের, নতুন সম্ভাবনার।
প্রশ্ন হচ্ছে সংস্কার থেকে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বাদ দিয়ে সেটাকে শুধু রাজনৈতিক এলিট অংশের সংস্কারপ্রক্রিয়ায় কেন রূপ দেওয়া হলো? কোন দলের কতজন সংসদে গিয়ে বসবেন, সেই বন্দোবস্তটা করে দেওয়াটাই কি তাহলে সংস্কার? এই যে অভ্যুত্থানে ১৬৮ পথশিশু, ২৮৪ জন শ্রমজীবী, ১২০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিহত হলেন, তাঁরা কেন হারিয়ে গেলেন সংস্কারচিন্তা থেকে?
সম্ভবত সেটিই হতে পারত ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার ঘোষণা দেওয়ার সবচেয়ে সেরা মুহূর্ত। রাজনীতিতে মোমেন্টাম সব সময় আসে না। ব্যাপক জনসমর্থনকে ভিত্তি করে দেশজুড়ে সংগঠন গড়ে তোলার যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল, সেটা করতে ছাত্রনেতৃত্ব ব্যর্থ হয়। জনগণের দেওয়া ত্রাণসামগ্রী তারা ঠিকভাবে বিতরণ করতেও ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের প্রতি শর্তহীন যে জনসমর্থন সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে প্রথম সংশয় ও প্রশ্ন তৈরি হয়।
পুরোনো রাজনৈতিক শক্তিগুলো ঠিকই সেই শূন্যস্থান ধরে ফেলে। তারা অভ্যুত্থানের দলীয় মালিকানার দাবি নিয়ে আসতে শুরু করে। প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পদগুলোর ভাগ–বাঁটোয়ারা শুরু হয়। বিএনপির দিক থেকে নানা সময়ে অভিযোগ করা হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো জামায়াতপন্থীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে বিএনপির নেতা–কর্মীরা আওয়ামী লীগের ফেলে যাওয়া হাট, বাজার, ঘাট, পরিবহন খাত দখল নিতে শুরু করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির নানা অভিযোগ উঠতে থাকে। দলীয় অন্তঃকোন্দল, সংঘাত ও খুনোখুনির ঘটনাও ঘটতে থাকে। সবখানে সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আওয়াজ উঠলেও পুরোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বন্দোবস্তই ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় আমলাতন্ত্র আবারও ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসে।
অন্যদিকে সারা দেশে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের সামনে রাজনৈতিক দিশা না থাকায় খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা দিশাহীন হয়ে পড়েন। নানা গোষ্ঠী তাঁদের অনেককে ব্যবহার করতে শুরু করে। বদলি–বাণিজ্য, তদবির–বাণিজ্য, মব সহিংসতা থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি ধীরে ধীরে এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে অনেকে জড়িয়ে পড়তে থাকেন।
সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রশ্রয়ে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো নিজেদের এতটাই শক্তিশালী ভাবতে শুরু করে যে মাজার ভাঙা থেকে শুরু করে নারীর চলাফেরা, পোশাক নিয়ে হেনস্তা ও আক্রমণের ঘটনা বাড়তে থাকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সমাজে এর প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। ছাত্রদের কারও কারও দিক থেকে এমন সব মন্তব্য আসতে থাকেন, তাতে জনমনে এই ধারণা জন্ম হতে থাকে যে কোনো কোনো মব সহিংসতার পেছনে ছাত্রদের সমর্থন আছে। এসব ঘটনায় অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামটাই বিতর্কিত হয়ে পড়ে।
এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্ররা যখন নতুন দল এনসিপির ঘোষণা দিলেন, ততক্ষণে অনেকখানি জনসমর্থন তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। পাঁচ তারকা হোটেলে ইফতার পার্টি নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা দিলেও নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রশ্নে জোরালো অবস্থান নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থান নিয়েছে, যেটা দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের অবস্থানের সঙ্গে মিলে যায়। মার্চ টু গোপালগঞ্জের মতো এমন কিছু কর্মসূচি নিতে যায়, যেটা তাদের নিজস্ব কর্মসূচি নাকি অন্য কারও এজেন্ডা বাস্তবায়ন, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।
জাতীয় রাজনীতিতে সরব হলেও নিজস্ব কর্মসূচির ভিত্তিতে দল গোছানোর মূল কাজটিই এনসিপিকে করতে দেখা যায়নি। বরং নতুন বন্দোবস্তের কথা বললেও রাজনৈতিক চর্চায় পুরোনো বন্দোবস্তের পথে হাঁটতেই দেখা গেছে দলটিকে। ফলে এনসিপি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কোনো রাজনৈতিক ধারা হিসেবে বিকশিত হতে চায় কি না, সেটা বড় একটা প্রশ্ন। জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করায় এনসিপিকে নিয়ে আরেক পশলা সমালোচনা শুরু হয়। সর্বশেষ খবরে জানা যাচ্ছে, এনসিপি আসন সমঝোতার জন্য বিএনপি ও জামায়াত দুই দলের সঙ্গেই আলোচনা করছে। এনসিপির কাছে মধ্যপন্থার রাজনীতির অর্থ কি তাহলে কোন দলের সঙ্গে আসন সমঝোতায় সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে, সেটা চিন্তা করে কোনো একদিকে হেলে পড়া?
এ সবকিছুর পরও আট মাস বয়সী রাজনৈতিক দলের দোষ-বিভ্রান্তি নিয়ে যেভাবে আলাপ চলছে, তাতে মনে হতেই পারে, পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক পথে চলছে, আর সব দোষ করে চলেছে এনসিপি। এর একটা উত্তর খুঁজতে হবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ভেতরে। আমাদের ভাবনাকাঠামোয় সাদা-কালোর বাইরে গিয়ে গ্রে জোনের অস্তিত্ব একেবারেই নেই। এখানে হয় কেউ দেবতা, না হয় দানব। সে কারণেই প্রথম পর্যায়ে ছাত্রনেতৃত্বের ভুলগুলোকে সমালোচনার চোখে দেখা হয়নি। বরং সবখানেই প্রশংসার জোয়ারে তাদেরকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের পক্ষে এমনভাবে বয়ান তৈরি করা হয়েছে, যেন তারা সব ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে। কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বয়ানটি পুরোপুরি বদলে গেছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলতাফ পারভেজ তাঁর জুলাই সনদে ‘জুলাই’ কোথায় শিরোনামের কলামে প্রশ্ন তুলেছেন, ‘কিন্তু জুলাই সনদে কী পেলাম আমরা। সেখানে কি আদৌ প্রত্যাশার “জুলাই” আছে? ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবসংবলিত জুলাই সনদ সবার পড়া উচিত। নিশ্চয়ই অনেকে সেটি পড়েছেনও। এই সনদে সর্বসম্মত অংশে কৃষক, শ্রমিক, দলিত, সংখ্যালঘুদের জীবনযাপনের প্রাত্যহিক বৈষম্য কমানোর সঙ্গে সরাসরি জড়িত কোনো সংস্কার প্রস্তাব আছে কি? না থাকলে কেন নেই?’
প্রশ্ন হচ্ছে সংস্কার থেকে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বাদ দিয়ে সেটাকে শুধু রাজনৈতিক এলিট অংশের সংস্কারপ্রক্রিয়ায় কেন রূপ দেওয়া হলো? কোন দলের কতজন সংসদে গিয়ে বসবেন, সেই বন্দোবস্তটা করে দেওয়াটাই কি তাহলে সংস্কার? এই যে অভ্যুত্থানে ১৬৮ পথশিশু, ২৮৪ জন শ্রমজীবী, ১২০ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিহত হলেন, তাঁরা কেন হারিয়ে গেলেন সংস্কারচিন্তা থেকে?
পরিস্থিতি এমন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাঞ্জাখোর তকমা দিয়ে পিটিয়ে হকার উচ্ছেদ করছেন ডাকসুর নির্বাচিতরা। ১৪ মাসের মাথায় বৈষম্য শব্দটাকে এভাবে প্রহসনে পরিণত করার অর্থ কী?